স্বীকার, অস্বীকার অথবা অভিব্যক্তি- শতানীক রায়
যখন আলোকে আপত্তি করার যথেষ্ট কারণ আছে
কবি- রমিত দে
প্রকাশক- বৈভাষিক
দাম- ১০০ টাকা
দাম- ১০০ টাকা
প্রত্যেকবার একই কবিতার কাছে কীভাবে ফিরে আসছি? বড়ো বিস্ময়কর এই বোধের কাছে তাহলে বোধহীন বেঁচে থাকা আমার
কতটা বোধের অতিরিক্ত কিংবা সঠিকতর মগ্নতার কাছাকাছি যেতে পারা, এটা নিয়ে বড্ড সংশয়ে পড়তে হয়। দোদুল্যমান অবস্থা থেকে কবিতার জন্মমুহূর্তে
পাঠক হিসেবে আমি তো কখনও পৌঁছতে পারি না কেবল অনেক পরে গিয়ে দেখি কতটা গড়ে উঠে তা
আস্ত একজন মানুষের মতো হয়ে উঠেছে। সংবেদ মাখানো শব্দ তো আর পাশাপাশি বসিয়ে কবিতা
লেখা হয় না। যদি সত্যিই একটা কবিতা যাপনের সঠিক অর্থে গজিয়ে উঠে নিজেকে যথার্থ
কবিতা হিসেবে ধরা না দিয়ে সম্পূর্ণ একটি কবিতা হয়ে ওঠে তা পড়ার সময় অনুভব করা যায়
যে, তার মধ্যে কবি রক্তমাংসে কতটা আছেন। শুধু এখানেই নয় সেই
শব্দগুলো অনুধাবন করতে গিয়ে সেগুলোকেই আয়নার মতো করে প্রতিফলিত করানোকে আমি পাঠক
হিসেবে পূর্ণাঙ্গ একটি যাত্রার ভেতর দিয়ে গিয়ে একটি কবিতার যথার্থ পাঠের কথা ভাবি।
এবং একটি কবিতা যদি এ সমস্ত যথাযথভাবে পূরণ করে তবেই সে কবিতা পাঠ এবং যাপনের
কাছাকাছি গিয়ে আত্মউন্মোচন ঘটাবে কবির এবং পাঠকের। এমন এক জটিল জায়গায় অবস্থান করে
কবি রমিত দের কাব্যগ্রন্থ "যখন আলোকে আপত্তি করার যথেষ্ট কারণ আছে"
পড়েছি।
নিজেকে দ্যাখার
যে গভীর ও অলৌকিক একটা দিক থাকে তা এই কাব্যগ্রন্থ পড়ে অনুভব করেছি। তবে একটা
জিনিস স্বীকার করতেই হয় যে, কোনও চেতনাই মৌলিক হয় না
পৃথিবীতে কেউ না কেউ সেটা ভেবেছেন এবং কালক্রমে তা আমাদের মনে এসে ধরা দেয়। এ
বইয়ের ক্ষেত্রেও এটা বিশ্বাস। এ বইয়ের প্রথম কবিতা পড়া যাক : 'এত দিন ধরে খুঁজে বেড়ানো আয়নাকে পাওয়া গেছে/ এই আমার প্রথম দুঃখ.../ এখন
আমার সামনে একটি মাংস/ আর মাংসের সামনে আমি মৃতদেহ/ ফুল গোঁজা দুজনের কোটেই।/ হাঁ
করে চেয়ে রইল যে/ সে হাত বাড়ালোনা/ যে হাত বাড়ালো সে কাচের থেকে ক্রুশ বানাবে
বলে.../ কাঠগুলোর কী হবে?/ এত বড় বড় গাছ/ এত বড় বড় পাতা/
তুমি কেবল পাতার ওপরের পাখিদের কথা ভাবছ!/ তুমি কেবল গাছের ওপরের কথা ভাবছ!'
কবি একবার নিজেকে সরাসরি দেখছেন কিন্তু আড়াল করছেন। অস্তিত্বের
মাইনর জায়গায় নিজের অবস্থানকে নিম্নবর্গ করে যে ছোটো একটা টুকরো থেকে দ্যাখা যায়
নিজেকে তার ভেতর এক অনন্য সুখ এবং দুঃখ দুটোই থাকে। যতটা খুঁজে পাওয়ার ভেতরে আরাম
বোধ থাকলেও আড়ালের প্রকট হয়ে ওঠা একটা সংকটও বটে, এখান থেকে
দুঃখও হয়। পরস্পরবিরোধি শোনালেও এটাই আসল ঘটনা। এই ডিসকোর্সের বোধের অংশবিশেষ আমরা
রোলাঁ বার্তের চেতনার মধ্যে পাই। বার্তের যেকোনো বোধের ভেতরেও দ্বন্দ্বের এমন
সংঘাত দেখি যে, সম্পূর্ণ বোধের বিকিরণ লুপ্ত হয়ে বিচিত্র
একটি অবলোকিত দ্যাখা তৈরি হয় যার ভেতর থেকে আত্মজৈবনিক বোধটুকু মার্জিত করে বোধকে।
সৃজন হয়ে ওঠে একাধারে জীবন, জীবনও হয়ে ওঠে সৃজনের অপর পিঠ।
রমিত দের কবিতায় প্রতিফলিত হচ্ছেন কবি এবং পাঠক দুজনেই। আয়নাই কি তাহলে মাধ্যম হতে
পারে সত্যের অনুসন্ধানে। রমিত দের জীবনহীন ম্লান হয়ে যাওয়া মাংস অন্তর্বোধের
প্রতীক যার সহযোগে তিনি সম্ভবত হেঁটে যাচ্ছেন বিচ্ছিন্ন অস্তিত্বের কাছাকাছি যা কি
না একজন রমিতকে আরেকজন রমিতের সামনাসামনি এনে দাঁড় করায়।
কাব্যগ্রন্থের
আরেকটি কবিতায় দেখি : 'প্লাতেরো নয়, একটা
খেলনা প্লাতেরো/ নিজেকে উপহার দিয়েছিল হিমেনিথ।/ এখন রমিত যদি একটা খেলনা রমিত দেয়
নিজেকে!/ রে রে করে তেড়ে যাবে।/ বলবে, আছেটা কী তোমার?/
না আছে ছোট ছোট জিন।/ না ছটা ফুলদানি/ না ফুলদানিতে গোলাপ.../ আছেটা
কী তোমার?/ এতদিন শুধু রমিতের স্বপ্ন দেখেছিল খেলনা।/ একদিন
চাঁদ উঠেছে কিন্তু তারা ওঠেনি/ একদিন রাস্তা থাকতেও কেউ বসে পড়েছে ঘাসে/ এমন একদিন
সে নিজের ঘরে নিয়ে গেল/ বলল, সূর্যটা ঠিক যত তাড়াতাড়ি উঠে
আসছে/ ঠিক তত তাড়াতাড়ি উঠে আসছে/ ঠিক তত তাড়াতাড়ি ঢুকে পড়ো আমার মধ্যে।' আত্মপ্রেম, রতি এবং দংশনের ভূমিকায় শরীর যখন আরও
শরীরগুলোর উপর নির্ভর করে নিজের কাছাকাছি পৌঁছায়। তাহলে রমিত এবং খেলনা মুখোমুখি
থেকে অস্তিত্বের সংঘাত তলোয়ারের থেকেও ধারালো। মদীয় আমেজ ডেকে আনে। পাঠক হিসেবে
কোনো কোনো সময় পুনঃপাঠের সময় নৈর্ব্যক্তিক মনে হলেও তাতে বুনোটের শিথিলতা আর
চেতনার বুননশিল্পর শিথিলতাও প্রকাশ পেয়েছে। প্রথম পাঠেই যে কবিতার বোধকে স্পর্শ
করার ছল করে বসেছিল এই পাঠক তা কি কবির প্রকাশের সহজতার ফল নাকি কবিতার ভিতরে
প্রবেশ করার পথ অবাধের ফল! এর মীমাংসায় কখনই যাব না। বরং সমস্ত মেদ সরিয়ে মুখোমুখি
দাঁড়ায় রমিত নিজেই। পাঠকও তখন রূপান্তরিত হয় রমিত কিংবা খেলনা রমিত-এ। অদ্ভুত
যাতায়াত। 'আছেটা কী তোমার?'-এর মতো
উদার প্রবাহ খুলে দেয় অনন্ত শাশ্বত পথের দরজা।
কাব্যগ্রন্থটির
একটি অদ্ভুত 'ভাবা'-র ওপর দাঁড়িয়ে আছে।
তাহলে তো বলতে হয় কবিতা বলতেই দ্যাখা এবং ভাবা। অবশ্য 'দ্যাখা' প্রক্রিয়াটির ওপরেই ভাবা প্রক্রিয়াটি এসে যায়। একজন ভাবুক যে সত্যিই ভাবেন
এটা ভেবে কিন্তু সে কখনও ভাবে না। অদ্ভুত আচরণ তাহলে কি এই ভাবার ওপর চাপিয়ে সেই
প্রক্রিয়াকে দাগিয়ে দেওয়া হবে! রমিত দের এই বইটা সম্পর্কে একটা 'অদ্ভুত ভাবা' যে জড়িয়ে আছে সেটা হয়তো পাঠক হিসেবে
আমি স্বীকৃতি দিচ্ছি তবে কবি কিন্তু সেই ভাবাকে সাবলীল রেখেছেন এবং সে ক্রিয়ার
প্রভাব কোনোভাবেই ভাষাকে জটিল করে তোলেনি, বরং আরও শিথিল
হয়েছে ভাষা : 'তুমি কেবল পাতার ওপরের পাখিদের কথা ভাবছ!/
তুমি কেবল গাছের ওপরের ফুলেদের কথা ভাবছ!' এমনটাই তো হওয়া
উচিত তবেই মূল চিন্তার এই মোহহীন প্রকাশ সম্ভব না হলে ভাষা তৈরির দিকে এগোলে এই
মূল চেতনা লুপ্ত হয়ে যেত, কবিকে তাঁর সৃষ্টি দিয়ে কখনই চেনা
যেত না। সরে আসাই ব্যক্তিচরিত্রের দ্বন্দ্বের প্রতীক। আবার আরেকটা দিক থাকে,
কোনো কবি ভাবছেন এমনভাবে যে, কবিতা লেখার
মুহূর্তটুকুই হয়ে ওঠে তাঁর ভাবনার অন্বেষণ কিংবা পূর্ণ প্রকাশের জায়গা। সেখানে
তিনি নিজের পথ তৈরি করে নিচ্ছেন কবিতার হয়ে ওঠার মধ্য দিয়ে। বিভিন্ন দিক থেকে
ভাবলেও এর মীমাংসা কোনোদিনই সম্ভব নয় কারণ, মানুষের মন
বিবর্তনশীল।
এই বইটির কবিতাগুলো
বিভিন্ন বিভাগে কিংবা শৈলীতে ভাগ করা যায়। আবার সূক্ষ্মভাবে যদি দেখি তাহলে বলতে
হয় 'সম্ভবত' শব্দটা জুড়ে দিয়ে একটি
সংশয় সৃষ্টি করাও যায়। কবিতাগুলোর ভেতর কোনো ধারাবাহিকতাও নেই। যেকোনো কবিতাই
স্বয়ংসম্পূর্ণ : কোনো যোগাযোগ নেই একে-অপরের সঙ্গে। ভীষণভাবে বিচ্ছিন্ন একটি
দৃষ্টিকোণ থেকে লেখা কবিতা।
একটি কবিতা না উল্লেখ করে পারছি
না : 'আমাকেও ফোন করে।/ যেমন ধরো সুব্রতদা, বৈদ্যনাথদা,
সমীরণদা/ তুষ্টি, অপূর্ব.../ জানতে চায় কেমন
আছি।/ যেমন ধরো গোপালদা, চিরঞ্জীবদা, আরও
বেশ কয়েকজন.../ ধরিনা। দেখি কাচের ওপর ভেসে উঠছে/ তুষ্টি... কলিং/ সমীরণদা
বহরমপুর... কলিং/ কলিং/ কলিং/ কলিং/ আমি সেই দাঁড় করিয়ে রাখা ব্রোঞ্জের মূর্তি/ যে
কিছুতেই জানবেনা নামের ভিতর সে নজরবন্দি/ আমি সেই দাঁড় করিয়ে রাখা ব্রোঞ্জের
মূর্তি/ যে কিছুতেই জানবেনা বাতাসেও উড়ছে তার কয়েক বিঘত।/ তোমার মুখ তো সূর্যের
দিকে/ আর ভেজা সেলাই মেশিনের অলৌকিক ভ্রমণে আমি।/ যার দেওয়ালগুলো এখন বেশ চওড়া/
যার দরজাটা কেউ নিয়ে পালিয়েছে/ দেখ, মাত্র একটি ঘন্টার জন্য
সে ঘুমিয়েছে।/ ঘুমন্ত শিশু।' আবারও এক বিচ্ছিন্নতা বোধে
আচ্ছন্ন একটি কবিতা যাকে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন দৃষ্টিকোণে অবস্থান করে না
অনুধাবন করলে বোধকে আয়ত্ত করা সম্ভব নয়। এবং সবেতেই একটি সম্ভবত কথা আরোপ করতে চাই
আমি। এখানে যেকোনো কবিতা নিয়ে আলোচনা করি না কেন তার মধ্যে কবির যাপন কখনই
প্রচ্ছন্নভাবে আলোকিত করা সম্ভব নয়। আবার এই কবিতাটিকে যাপনের ভেতর দিয়ে দেখতে
গেলেও বলতে ইচ্ছে করে, সম্ভবত এর ভেতর একটি আড়াল আছে,
যাপনের অন্তরালে আরেকটি যাপন যা কি না যাপন দিয়ে আড়াল করার চেষ্টা।
আড়াল করার চেষ্টা না থাকলে এমন অস্বীকারের বোধ কাজ করে না কোনো মানুষের মনে। তাহলে
কী বলব এ হেন বেঁচে থাকাকে? কিছু নির্ণয়ের প্রয়োজনই নেই।
জীবন তো বয়ে চলা থেকে আসে। যা আমরা শুধু ধরতে চেষ্টা করি মাত্র। এত কিছু বলার পর
আর বেশি দূর এগোব না কারণ, রিভিউতে এর বেশি বলব না। পাঠক
বইটি বেশি করে পড়ুন আর পুনরায় আলোচনা করুন। যে কোনো বইয়েরই একাধিক দৃষ্টি থেকে
আলোচনা হওয়া প্রয়োজন তাতে আলোচনার ব্যপ্তি বাড়ে।
- শতানীক রায়
আঙ্গিক, বইমেলা সংখ্যা, ২০১৯





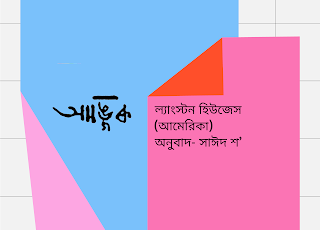
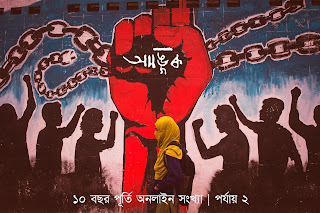
মন্তব্যসমূহ
Rituparna