আয়না ও এক লাইনের বাইরের জীবন- তাপস বিশ্বাস
অ্যাসাইলামের ডায়ারি
লেখক- অদ্রীশ বিশ্বাস
ধানসিড়ি, প্রকাশ জানুয়ারি ২০১৮
দাম- ১৫০ টাকা
দাম- ১৫০ টাকা
'স্বয়ং হ্যামলেট'
"ইমেজ রক্ষা নয়, ইমেজকে
আক্রমণ করাই ছিল তাঁর লক্ষ্য। কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন আজকের লেখকের মাথার চারপাশে
কোনো জ্যোতির্বলয় নেই। সে আর 'হ্যামলেট'- এর রচয়িতা নয়, স্বয়ং হ্যামলেট। যে তার
কথা বলে। তাই হ্যামলেট পুননির্মিত হয়। ...... আজকের হ্যামলেট পুরোনো হ্যামলেটের সংস্কারকে ভেঙে
একটা অন্য টেক্সট হাজির করে যা বাংলা ভাষায় সেভাবে দেখা যায়নি।" — এমনই
লিখেছিলেন অদ্রীশ বিশ্বাস। ২০০৯ সালে তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত 'সন্দীপন
চট্টোপাধ্যায়ের ডায়েরি'-র ভূমিকায়। প্রায়
৮ বছর পরের কাছাকাছি সময়ে— "কখনও
আক্রমণ নিজেকে, নিজের চারপাশকে, যা হওয়ার কথা ছিল অথচ হতে পারছে না বলে। সমাজ একটা
আজব চিজ, সেটা দেখানো আর তার জন্য কতকিছু না পারার বেদনা আমাদের আত্মপ্রকাশে বাঁধা
হয়ে দাঁড়ায়। কিংবা গণতন্ত্রে বাঁধা। পাগলামিতে বাঁধা। সৃষ্টিতে বাঁধা। যা চায়
মন, তাকে এভাবেই নানা অপ্রকাশ আটকে ধরে এক লাইন লেখার মধ্যেও। অপারগতা যন্ত্রণার।
এমনকি এক লাইনের হলেও। ....... এভাবেই চলে এবং চলুক এক লাইন। নো জেব্রাক্রসিং। বাণী সংগ্রহ নয়,
বাংলায় এমন বই প্রথম।" — নিজেই লিখে রেখে যান অদ্রীশ তাঁর 'অ্যাসাইলামের
ডায়ারি'-র অন্তর্গত 'এক লাইন'- অংশের ভূমিকাস্বরূপ। পূর্বের
সম্পাদক এখানে স্বয়ং লেখক। "সে আর 'হ্যামলেট'-এর রচয়িতা নয়, স্বয়ং
হ্যামলেট।" প্রায় একই সুতোর দু'তরফের মাথায় বাঁধা সমপ্রসঙ্গের গিঁটটিতে ধরা
থাকে চেতন-অবচেতনে ঘটতে থাকা "অপারগতা যন্ত্রণার" জট। তবে কি অদ্রীশ
পূর্ব থেকেই সচেতন? তবে কি অগ্রজের হাত ধরে উঠে এক সুবৃহৎ ঘোষনার আগেই মাথায়
গোছাতে থাকেন ঝড়? কিছুটা কৌনিক হলেও, অগ্রজের কল্পচর্চায় সদাব্যস্ত এক মৃত্যুবিলাস
এক্ষেত্রে কি প্রবল ভারী ছায়ায় খুলে রাখছিল একটা ঘন শাদা চোখ, যে রাতে 'শুয়ে
থাকা মানুষের মাঝখানে' জেগে বসে দেখতে পায়—
'রোগীরা রাতে শুয়ে পড়ার পর
মাসিরা সাপলুডো খেলে।'
'রোগীরা রাতে শুয়ে পড়ার পর
মাসিরা সাপলুডো খেলে।'
'আয়না
নেই' — আয়না
সত্যিই কি নেই ?
২৮
নভেম্বর ২০০৫- এ (সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের ডায়েরি) সন্দীপন লিখেছিলেন — "বাড়িতে
ফুল সাইজ আয়না নেই। এসব অভিনেতাদের লাগে এতদিন ভেবেছি, আজ স্নানের আগে ন্যুড হয়ে
নিজেকে একবার দেখতে ইচ্ছে করল। নগ্ন ইচ্ছে। ......আমি বাথরুমের দরজা বন্ধ করে দিয়ে
আয়না ছাড়াই নিজেকে দেখি আর ভাবি আবার কবে দেখা হবে।" 'অ্যাসাইলামের
ডায়ারি'-তে দিনপঞ্জির আশ্চর্যজনক অনুল্লেখ ঘটলেও (যদিও পঞ্চাশ পৃষ্ঠায়
সামগ্রিকভাবে এই ডায়েরির একটি তারিখ ও রচনা-স্থানের উল্লেখ আছে) বইয়ের ৪৮
পৃষ্ঠায় দেখা যাচ্ছে অদ্রীশ বিশ্বাস লিখছেন—
'ওয়ার্ডে
কোথায়ও
কোনো
আয়না নেই।' সন্দীপন নিজেকে দেখে নিতে চাইছেন — "হিরণের (হিরণ মিত্র/ সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের বহু বইয়ের প্রচ্ছদশিল্পী ও লেখকের একাধিক পোর্ট্রেটের স্রষ্টা) আঁকা লেখকের ন্যুড মলাট"-এ, যে বইয়ের সম্পাদক স্বয়ং অদ্রীশ বিশ্বাস। আবার সেই অদ্রীশ-ই আয়নার অভাবে নিজেকে দেখে নেন—
'ডে- কেয়ারের বন্ধ
জানালার কাচ'-এ।
'ওয়ার্ডে
কোথায়ও
কোনো
আয়না নেই।' সন্দীপন নিজেকে দেখে নিতে চাইছেন — "হিরণের (হিরণ মিত্র/ সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের বহু বইয়ের প্রচ্ছদশিল্পী ও লেখকের একাধিক পোর্ট্রেটের স্রষ্টা) আঁকা লেখকের ন্যুড মলাট"-এ, যে বইয়ের সম্পাদক স্বয়ং অদ্রীশ বিশ্বাস। আবার সেই অদ্রীশ-ই আয়নার অভাবে নিজেকে দেখে নেন—
'ডে- কেয়ারের বন্ধ
জানালার কাচ'-এ।
এখন
প্রশ্ন থেকে যায় নিজের ভেতর ভেঙে যাওয়া বন্ধ কাচে সমগোত্রীয় মানুষ কাকে দেখেন? এর
উত্তর কি কোনো চেতনার সুদৃশ্য ঝলমলে হাতে থাকে! না। থাকে না নিশ্চিতভাবেই।
অ্যাসাইলাম থেকে, ভ্যান গঘ ভাই থিও-কে লিখেছিলেন, 'আসলে ভেঙেচুরে এমন ধ্বংস হয়ে
গেছি যে বাইরে গিয়ে দাঁড়াবার ক্ষমতা নেই।' আর ঠিক তখনই মাথার নরম থকথকে ব্যারেন ল্যান্ডে হঠাৎ পেকে ওঠা
ধান বাইরের দাঁড়ানো পৃথিবীর নবান্নের দিকে থুথু ছুঁড়ে বলে ওঠে—
'স্যার,
একটা ত্রিশূল পেলেই
সব ধ্বংস করে দেব'।
কার্যত, তার চেতনমুখ যখন তাকে দিয়ে বলিয়ে নেয়—
'স্যার, একটা মাংস পিস বেশি দিতে বলবেন,
আমি শক্তি অর্জন করতে চাই।'
'স্যার,
একটা ত্রিশূল পেলেই
সব ধ্বংস করে দেব'।
কার্যত, তার চেতনমুখ যখন তাকে দিয়ে বলিয়ে নেয়—
'স্যার, একটা মাংস পিস বেশি দিতে বলবেন,
আমি শক্তি অর্জন করতে চাই।'
এই
পর্যন্ত এসে যুক্তি দাঁড়িয়ে যায় — মৃত্যুর শাদা বাক্যের মতো, একা। অতীতের ছাঁচ
গড়িয়ে নামে না-হওয়া তুলনার মৃদু গড়নের দিকে। সত্যি তুলনা কি হয়? একটু নেড়ে
দেখব সেসব।
হাতে নীল বিষের থলি
নিয়ে আসা সন্দীপনের দিকে তখন আঢ়চোখে তাকাচ্ছে না আর কেউ। ততদিনে নীল থলিগুলোর মুখ
থেকে বেরিযে আসা অমৃতের গন্ধ রাজপথে মুখে মুখে ঘোরাঘুরি করছে 'প্রকৃত পানীয়'-র
মতো। আর প্রতিষ্ঠান ভাঙতে ভাঙতে নিজেকেই প্রতিষ্ঠান ভেবে ফেলা সন্দীপন, তখনও সেই
শুরুর মতোই অক্লান্ত, তখনও নিজেকে ক্রমাগত ভেঙে চলেছেন ঠিক সেইভাবে, যেভাবে স্যাডিজমের
নীল বিষে ডোবানো কোনো প্রতিরোধহীন মানুষ সর্বপ্রথম ও সর্বশেষ নিজেকেই ভাঙেন। তবে
এই ভাঙনটি হয়ত ভ্যান গঘের মতো অতটাও অসচেতন নয়, যা মানুষকে অ্যাসাইলামের দিকে
টেনে নিয়ে যায়। এখানেই ব্যক্তির এক সচেতন ভাঙনের সাক্ষী হতে থাকে 'হারাধনের কয়েকটি
সন্তান', 'নিষিদ্ধ স্বপ্নের ডায়েরি'-রা। যা, অদ্রীশের নিজের কথায়, "এই
ডায়েরির পাতায় সন্দীপনের কোনো পূর্ব-সংস্কার নেই শুধু নয়, তিনি দুঃসাহসী, অকপট,
আনপ্রেডিকটেবল। কোনো কথা লিখতেই কোনো সংশয় নেই। যা ভাবছেন লিখছেন। ......এমনকি
নিজের সম্পর্কেও ভয়াবহভাবে অকপট।" আর
ঠিক এখানেই আমাদের আলোচনার পয়েন্ট অফ ইন্টারেস্টটি কিছুটা নিহিত থাকে। হলেও
সম্পাদনা, ছাপার অক্ষরে অদ্রীশের প্রথম কাজ সম্ভবত আসছে ১৯৯৯-এ (আন্দ্রেই তারকোভস্কি
সম্পর্কিত)। আর ২০০৩ সালে প্রকাশিত তাঁর 'গদ্য সমগ্র -১' -র ভূমিকায় সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়
লিখছেন — "প্রায় ৪০ বছর ধরে এইসব লেখালেখির শবযাত্রা অবশেষে গন্তব্যে
পৌঁছালো। যদিও সমগ্র গদ্য ঠিক নয়, অনেক খই-বাতাসাও রাস্তায় পড়ে রইল। এদের ইহলৌকিক
সৎকারের যাবতীয় তোড়জোড় করেছেন প্রথম দিকে অদ্রীশ বিশ্বাস, মাঝখানে প্রচেতা ঘোষ......।"
অর্থাৎ সম্পাদকের সেই প্রবল ঋজুস্বত্ত্বা গঠনের প্রথম দিকের দিনগুলির অনেকটা জুড়ে
অদ্রীশ যে সন্দীপনে আচ্ছন্ন ছিলেন, একথা সহজেই অনুমান করা যায়। চিরকাল মিথভাঙা
বিষয়ের দিকে ছুটে যাওয়া ব্যক্তি অদ্রীশ, নিজের ভেতর ভেতর, বাইরের স্বাভাবিক স্রোত ও ঘূর্ণীর বিপরীতে দৃঢ় পা রাখা অদ্রীশ, এক সমান্তরাল
ব্যক্তি-দাহকার্যের মানুষকে নিজপুষ্টির কারণে আত্মস্থ করবেন না, দূরে সরিয়ে
রাখবেন, এখানে অন্তত এমন ভাবনার কোনো অবকাশ থাকে না। কার্যত, সন্দীপনের সিরিয়াস
পাঠক মাত্রই জানেন, সন্দীপনের প্রায় সারাজীবনের লেখালেখি কেবলমাত্র ও কেবলমাত্র
শুধু এক ব্যক্তিভাঙনের দিকেই মুখ তুলে থাকে। সেইসব দাহক্রিয়ার নিরুচ্চার উল্লাস,
ভাঙনের নিষিদ্ধ অনুভূতিমালার এক নিবিড় সাক্ষী হয়ে বড় হতে হতে সম্পাদক, লেখক ও
ব্যক্তি অদ্রীশ বিশ্বাস নিজেও কি বসে থাকেননি এক "রক্ত-ঘাম-অশ্রু-বীর্য
মাখা" ধ্বংসের দিকে মুখ করে? অকপট স্যাডিজিমের নীল বিষে প্রভাবিত হয়নি কি কোনো
নির্জনতার একাকী খোপ? অদ্রীশ নিজেই লিখছেন-
'পাগলের
এঁটোকাঁটা খেয়ে
যে কুকুরেরা বাঁচে
তারাও কি একদিন
পাগল হয়ে যাবে' সুতরাং, আয়না থাকে। আয়না থাকছেও। এখানে তা থাকছে এক 'জরুরি আবিষ্কার' ধরে। জেগে ওঠার আগে মানুষ শুধু তার সামনে 'আদার আইডেনটিটি হয়ে শুয়ে থাকে।'
'পাগলের
এঁটোকাঁটা খেয়ে
যে কুকুরেরা বাঁচে
তারাও কি একদিন
পাগল হয়ে যাবে' সুতরাং, আয়না থাকে। আয়না থাকছেও। এখানে তা থাকছে এক 'জরুরি আবিষ্কার' ধরে। জেগে ওঠার আগে মানুষ শুধু তার সামনে 'আদার আইডেনটিটি হয়ে শুয়ে থাকে।'
এক
লাইনের বাইরের জীবন
অদ্রীশ
বিশ্বাসের জন্ম ১৯৬৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে। বাংলা সাহিত্যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
থেকে স্নাতকোত্তর ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ঐ বিষয়েই ডক্টরেট। অদ্রীশের এক
সহপাঠীর কথায় "বাইরে ইমোশন কম দেখালেও, ভিতরে ভিতরে ভারী অভিমানী ছিল অদ্রীশ।
আর, খুব অল্প হলেও, ক্বচিৎ-কদাচিৎ তার একটা প্রকাশ ঘটে গেলে আমরা তার হাস্যোজ্জ্বল
ব্যক্তিত্বের সঙ্গে তার এই বেদনাঘন রাগকে মেলাতে পারতাম না।" বন্ধুর কথাতেই
জানতে পারি, "বহু প্রবন্ধ লিখেছে অদ্রীশ, যথার্থ একাডেমিক সেসব লেখা,
গবেষণায় এতটুকু ফাঁকি নেই। সারাজীবন যদি সে একটি বিষয়েই গবেষণা করে যেতে পারত,
তাহলে বোধহয় খুশি হত সে, কারণ বহুপল্লবায়িত হওয়ার তুলনায় গভীর সমুদ্রে ঝাঁপ
দেওয়ার প্রবণতা ও আগ্রহ তার বেশি ছিল"। এ এক যথার্থ মন্তব্যই বটে। 'বটতলার বই:
উনিশ শতকের দুষ্প্রাপ্য কুড়িটি বই' (২০১১/ গাঙচিল)- এর সম্পাদনায় এক দুঃসাধ্য
গবেষণা তাঁর ব্যক্তিত্বের এই দিকটিকেই ইশারা করে। বিশেষত ইন্টারনেট বর্জিত সেই
বইয়ের যে যুগ, সেখানে ঢুকে, মণিমুক্তো তুলে এনে নতুন যুগের পাঠকের সামনে তুলে ধরার
যে অসাধ্য সাধন তিনি করেছেন বা করার সাহস দেখিয়েছেন, এক দিক থেকে দেখলে, তা এক প্রচন্ড
একগুঁয়ে, অনড় তথা বিপরীতমুখী মনস্তত্ত্বের দরজা খুলে রাখে। যে বিষয়ে অদ্রীশ কাজ
করেছেন, তা সে সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের গদ্য হোক বা বাংলা সাহিত্যে শ্লীল-অশ্লীল
নিয়ে গবেষণা — "একেকটা বিষয় নিয়ে ডুবুরির মতো কাজ করেছে অদ্রীশ।"
এহেন
একজন অদ্রীশ বিশ্বাসের ভেতরেই কি তাহলে পোঁতা থেকে যাচ্ছে না এক সুবৃহৎ সিস্টেম
ভেঙে দেওয়ার বীজ? জীবনের স্বাভাবিক স্পন্দনকে অগ্রাহ্য করার মারণ-জিন কি খোলা
থাকছে না কোথাও? কোথাও কি একটা বৃহৎ অ্যাসাইলামের মুখ হা হয়ে থাকছে না? 'অ্যাসাইলামের
ডায়ারি'-র অন্তর্গত 'এক লাইন' আসলে এক একটি সেইসব স্পার্ক, সেইসব বিদ্যুৎরেখা যা
মিলিয়ে যাওয়ার আগে এক বিরাট শব্দে ফেটে পড়ার সম্ভবনা তৈরি করে দেয়।
এই
আলোচনার শেষলগ্নে এবার আসি সেই অমোঘ জায়গায়। 'লীলাবতী'। মৃত্যুর ঠিক পরে পরেই প্রকাশিত,
মা'কে নিয়ে লেখা অদ্রীশের এক ক্ষীণতনু উপন্যাস ( অদ্রীশ বিশ্বাসের স্বেচ্ছা
মৃত্যুবরণ জুন, ২০১৭ আর 'লীলাবতী'র প্রকাশকাল সেপ্টেম্বর, 2018 / ৯ঋকাল বুকস,
সম্পাদনা: অদ্রীশ বিশ্বাস স্মৃতিরক্ষা কমিটি)। আশ্চর্যজনকভাবে, এই 'লীলাবতী'-ই
অদ্রীশের জীবনের প্রথম ও শেষ ক্রিয়েটিভ লেখা যেখানে— সাহিত্য, গবেষণা, সম্পাদনায়
তুখোড় একজন মানুষের যাবতীয় সমাজ, সাহিত্য, সংস্কৃতি, রাজনীতি তথা ব্যক্তিগতের
চেতনা ও বোধ, যেন একটা সরু মুখ পাচ্ছে। সমাজের সাথে যুক্ত হতে হতে একটা প্রগাঢ় ব্যক্তি-সচেনতাবোধ
আসলে চরম একাকীত্ব, পরম বিচ্ছিন্নতা ও অবসাদে ডুবে যাচ্ছে— এই সময়টিতে তারই একটা উদ্গীরণের
মুখ তৈরি হচ্ছে যেন। যা কিছুটা হয়ত ফেটেও পড়ছে উপন্যাসের পঁয়ত্রিশতম অধ্যায়ে—
"অনেক অনেক বছর পর রোমের বিশাল বড় কলোসিয়ামে দাঁড়িয়ে সকালের প্রথম আলোয়
অদ্রীশ বলে ওঠে, 'মেরে প্যায়ারে ভাইয়ো অর বহিনো, হামে দেখ লুঙ্গা।' চিরকাল
আবেগের অসংলগ্ন কেশরের ঝুঁটি শক্ত মুঠোয় ধরে রাখা ঋজু অদ্রীশ এখানে, প্রায় অপ্রয়োজনে
আবেগের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন। কিন্তু কেন? কেন এভাবে ভেঙে যাবে আগল? এই ফেটে পড়ার
উদ্যোগই কি তাহলে খুব নিচু পূর্বস্বর তৈরি করে রাখছিল অদ্রীশের মৃত্যুঘোষণার তথা 'লীলাবতী'-র,
মাত্র দুই বছর আগের লেখা (২১-০৭-২০১৫) 'অ্যাসাইলামের ডায়ারি'-তে? তবে কি 'অ্যাসাইলামের
ডায়ারি' কোনো বৃহত্তর ইঙ্গিত হয়ে আসে? নিজের ভেতর যাপন করা চন্দ্রাহত লীলাবতী তাহলে
কি আগেই ঢুকে পড়েছিল অ্যাসাইলামের অদ্রীশের ভেতর? সে উত্তর হয়ত 'লীলাবতী'ই জানে।
'অ্যাসাইলামের ডায়ারি' কেবল সেদিকের প্রবেশের একটা নিচু চোরাপথ ও তার ছোট ছোট
সিঁড়ি নির্মাণ করে রাখে। আর এখানেই ধরা থাকে অত্যন্ত দৃষ্টিমধুর প্রচ্ছদে ঢাকা বর্তমানের
দৃঢ়তনু বইটির সার্থকতা।
- তাপস বিশ্বাস
আঙ্গিক, বইমেলা সংখ্যা, ২০১৯



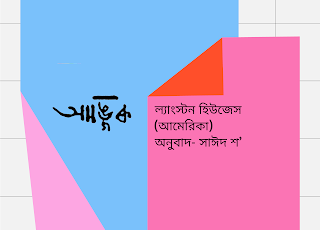



মন্তব্যসমূহ