বাংলা আত্মজীবনীকে ডিস্টার্ব করতে এসেছে- সম্বিত বসু
দাম- ১২৫ টাকা
সারাজীবনে কতরকমেরই অজুহাত না দিয়েছি। দিতে শুনেছি। ক্রিকেট খেলা চলছে পাড়ায়। গলিতে। সামনে একটি বাড়ির বাইরের বাথরুমঘর পড়ে।
কপাট ভেজানো। বাইরে থেকে বন্ধ করা যায় না। টেনিস বলে খেলা চলছে। ব্যাটসম্যান
মারল সপাটে। এ—দেওয়াল, সে—দেওয়াল ঘুরে বলটা
বাথরুমের দরজা খুলে সোজা পড়ল গিয়ে কমোটে। নিয়মমতো যে মেরেছে এই বল, তাকে তুলতে হবে। বাড়ি থেকে গামছা পরে যখন সে বেরল, বাধ
সাধল তার মা। বলল, ব্রাহ্মণ হয়ে এসব করা যাবে না। এই
অজুহাতটি অবশ্য আমার সেই বন্ধুটি কানে তোলেনি। কারণ এতো দস্তুরমতো বাজে অজুহাত!
কারণ অজুহাতের মধ্যে একধরনের বিশ্বাসযোগ্যতা থাকা জরুরি। আর জোরদার, বিশ্বাসওয়ালা অজুহাতটি কী, তা চিনিয়ে দিয়েছেন
রাণা রায়চৌধুরী। তাঁর ‘রাণার কথা’য়
লিখছেন–
‘আমি যে এখন লিখছি, এটা লোকজনকে বলতে আমার লজ্জা
করে।’
‘লিখছিলাম’ না লিখে রারাচৌ বলছেন–
‘মেঘ দেখছিলাম– মেঘ
হাবুদের আনন্দিত অট্টালিকার ওপর কাকের মতো বসে আছে, কিংবা
বললাম– গান শুনছি, দেবব্রত বিশ্বাস,
রবীন্দ্রসঙ্গীত। রবীন্দ্রসঙ্গীতের চেয়ে বড় অজুহাত আর কী আছে?’
একজন লেখক,
যে এই ঢাকপ্রধান বিশ্বে নিজের লেখার কথা বলতে চাইছে না। একান্ত ওই
সময় কী করছে জানাতে চাইছে না প্রশ্নকর্তাকে। যে সময় লিখছে, সেটা ‘নির্জন’। এমনকী, লেখার মাঝে যে ফোন এল, চিন্তাসূত্র ছিঁড়ে গেল
(কমার পরের বাক্যটা ধার করলাম কবি দীপ্তিপ্রকাশ দে’র কাছ
থেকে, দীপ্তি, কেমন আছো?) সেই সময়, সে গোটা লেখা থেকেই বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল।
লেখার লোক ও কথা বলার লোক আলাদা হয়ে গেল এই মুহূর্তে এসে। হাজিপাজি বলে তখন
ফোন রাখার চেষ্টা, গলি দিয়ে যাওয়া ভালমানুষ ও বিরক্তিকর
পড়শিকে উত্তর দিয়ে ফিরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা।
এখন লিখছি–
একথা বললেই, হাজারো প্রশ্ন। কী লিখছেন, কেন লিখছেন? কিন্তু
এই নির্জনে থাকা, সাধনার মতো করে থাকা তা এক আত্মীয়তার
জন্যই। চিরতরে একা বনে যাওয়া নয়। ‘আত্মীয়তা’ শব্দটি রারাচৌ—এর সঙ্গে মিশে আছে। উৎসর্গ একটু পড়ে
নেওয়া যাক এই তালে, সেই উৎসর্গ যা আমার কথাকে সাপোর্ট করবে–
ফেলে আসা পথের ধুলো,
তোমাকে।
বাঁশবন,
আত্মহত্যার দড়ি, ফুঁপিয়ে কান্না, তোমাকে।
পোস্টকার্ড,
টেলিগ্রাফের তার, টুনটুনি পাখি, তোমাকে।
লক্ষ্মীপুজোর প্রসাদ তোমাকে।
রাজীবপুর,
বাবার নস্যির কৌটো, তোমাদের।
ক্লাস সেভেন—এইট, রেডিও নাটক এবং শম্ভু মিত্র আপনাকেও।
গ্রামের সরকারি ডাক্তারখানা, মিক্সচারের শিশি তোমাকেও।
বাবার আদ্যাস্তোত্র পাঠ তোমাকেও।
অন্ধকারের দীর্ঘ শ্মশানযাত্রীগণ, আপনাদেরও।
জোনাকিপোকা,
ব্যাঙের ডাক, পুকুরে মাছের ঘাই তোমাদেরও।
নকশাল আন্দোলন,
বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ,
কংগ্রেস আমল—বামফ্রন্ট আমল আপনাদেরও।
প্রথম লাজুকতা তোমাকেও।
প্রথম নির্মলা মিশ্র আপনাকেও।
দ্বিতীয় ক্রোধ,
তৃতীয় ক্ষরণ, চতুর্থ মনঃকষ্ট,
প্রবল বর্ষণের রাত,
সুকান্ত ভট্টাচার্য,
আত্মীয়জ্ঞানে আপনাদের সবাইকে।
কাকে বলে ‘আত্মীয়জ্ঞান’? কেবলমাত্র রক্তের সম্পর্ক? বাজার যাওয়ার পথে স্কুটারে চড়া মামার মুখ? কারা
আত্মজন– এ নিয়ে জোরালো প্রশ্ন উঠতে শুরু করে জীবনে,
একটু বেলা হলেই। ছোটবেলা থেকেই যাদের চেনানো হয়, এরা তোমার আত্মীয়, তাদের সঙ্গে সখ্যের অভিনয় চলতে
থাকে সারাজীবন। কিন্তু যে পাঁচিলের উপর বসে দীর্ঘদিন রাস্তা দেখা, যে রাস্তায় ক্রিকেট খেলা, যে মুদীর দোকানে ধারের
খাতা থাকত, তারা কি আত্মীয় নয়? স্মৃতির
উপর যতই সদ্য— অতীতের প্রলেপ পড়তে থাকুক, সেই পুরনো আত্মীয়তা ক্রমাগত মনে পড়ে। কারণ মনে পড়ার উপরই তো নির্ভর
করে কারা আত্মীয়। যে শশব্যস্ত শামুক পঁাচিলে ওঠার চেষ্টা করছিল ভর সন্ধেবেলায়,
তাকে আমি দেখতে পেয়েছিলাম বঁা—পায়ের নখ
ভেঙে। ফুটবল খেলতে গিয়ে, সেই কোন ছোটবেলায়। তখনও জানতাম
না নখের দিক দিয়ে মারতে নেই। ওই নখ ভেঙে খুঁড়িয়ে বাড়ি ফিরতে গিয়ে দেখা হয়েছিল
সেই আত্মীয় শামুকের সঙ্গে। সেও খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে শ্যাওলার ঘরবাড়ি পেরিয়ে পাঁচিলের নিরক্ষরেখায় ওঠার চেষ্টাস করছিল। ব্যথার মধ্যে দিয়ে সেই শামুকের
যাত্রার সঙ্গে আলাপ আমি ভুলিনি। আমার কাছে সেই শামুক আত্মীয়সম। এই তথাকথিত ‘অনাত্মীয়’, যারা রোজকার জীবনের অংশ আছে বা ছিল।
এমনকী, নকশাল আমল, কংগ্রেস বা
বামফ্রন্ট আমলকেও আত্মীয়জ্ঞান করা হল। বোঝাই যাচ্ছে, লেখক
এখানে ‘রিসিভার’ বা ‘গ্রাহক যন্ত্র’ হয়ে পড়েছে। সময়কে সে ধারণ করেছে নিজের শরীরে, লেখায়। রং ও
দাগের কাটাকুটিতে। এই সমস্ত টুকরো জিনিসের সঙ্গে কাটানো রারাচৌ—এর সময়ই কি এই বইয়ের মূল সূত্র নয়? তার সঙ্গে
সঙ্গে জুড়ে যায় শারীরিক অনুভূতিমালাও!
‘আমি সারাজীবন চুপ করেই থাকতে চেয়েছিলাম। চুপ করে থাকাটাও এক ধরনের
প্রতিবাদ। তাই এই নির্জন রাত্রিতে মনে হয় সুখ আছে এক জিনিসে। কী সে? মনকে প্রসারিত করে এই অনন্তের অসীমতার সঙ্গে এক ক’রে
দেবার চেষ্টা করো। মনে ভাবো অনন্ত আকাশের এই অজানা প্রাণীদের সেসব কত অজানা
অদৃষ্ট ধরনের জীবনযাত্রা, কত সুখদুঃখ, কত
আনন্দ। সেসব কি অজানা উচ্ছ্বাস– তোমার মন অসীমতার রহস্যে
ভরে উঠবে। ক্ষুদ্রত্ব ভেসে যাবে অনন্তের অমৃতের জোয়ারে।’
উপরের এই উদ্ধৃতাংশের প্রথম দু’লাইন রারাচৌ লিখিত হলেও বাকি অংশ রারাচৌ—এর নয়। বাকি অংশ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘স্মৃতির
রেখা’ থেকে নেওয়া লেখার অংশ। দুম করে এই দুই লেখা জুড়ে
দেওয়া একান্তই আমার অনাবশ্যক বদমায়েশি। কিন্তু কোথাও কি সামঞ্জস নেই বিন্দুমাত্রও?
বিভূতিভূষণ লিখছেন–
‘অনন্ত যে তোমার চারধানে প্রসারিত, তোমার পায়ের
তলায় তৃণদলের শ্যামলতার, তোমার কোলের শিশুর মুখের হাসিতে,
তোমার আঙ্গিনায় পাখীর ডাকে, সন্ধ্যায়
ঝিঁঝিঁর সুরে, নৈশপাখীর আওয়াজে– কিন্তু
আমি শুনবো না। আমি দেখবো না, আমি চোখ বুজে আছি– এত কার স্পর্ধা আমার চোখ খোলে?’
চোখ খুলে রেখেছেন রারাচৌ। বলছেন–
‘এই পতঙ্গ, এই পোকামাকড় না থাকলে আমি থাকতাম না।
জীবন কীরকম বিস্বাদ লাগত যদি না আমার দেওয়ালের আরশোলা, টিকটিকিগুলো
না থাকত।... আরশোলার পায়ের চিহ্নে আঁকা থাকে আমাদের ঝুমার বিবাহকার্ড।’
বিভূতিভূষণের অনন্তের সঙ্গে, আরশোলার সঙ্গে ঝুমার বিয়ের কার্ডের সঙ্গে জুড়ে দিলেন
রারাচৌ। ঝুমা, আমাদের কাছের কেউ, নিকটাত্মীয়
কেউ নয় কি? তাঁর বিয়ের কার্ড মানে শুভেচ্ছাবার্তার সঙ্গে
আরশোলার পায়ের চিহ্ন আঁকা। মনে রাখতে হবে, এ হল সেই
আরশোলা, যাতে ঝুমা নামক মেয়েরা ভয় পেয়ে যেতে পারে।
চিৎকার করে স্বজনসকাশে দৌড় দিতে পারে। বিয়ের পরের যে আড়ষ্টভাব তা কেটে যেতে
পারে সামান্য আরশোলার ভয়েই।
গরিব মানুষ যখন খায়,
তখন তৃপ্তির ছাপ থাকে তার চোখেমুখে। গরিব মানে খেটে—খাওয়া মানুষ। দিন আনি দিন খাই মানুষ। তাদের খাবার হয়তো সাধারণ– পান্তাভাত। কিন্তু যে তৃপ্তির ছাপ, চিহ্ন– তা দেখে লোভ জাগে। এটা একটা অনুভূতির জন্য লোভ। খাদ্যের জন্য না। ভাল
রান্নার জন্য না, পরিমাণের জন্য না। রারাচৌ লিখছেন সেকথাও–
‘গরিব মানুষের খাওয়া দেখলেই আমার বারবার লোভ জাগত। যেন গরিব মানুষের
খাওয়াই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ খাওয়া।’
কিন্তু আফসোস এ কারণে নয়। আফসোস হয়–
‘এত বছর বাঁচলাম অথচ ফুলের, ফুলের পরাগ থেকে ফুটে ওঠা,
প্রস্ফুটিত হওয়া দেখলাম না।’
এমন ক’জন আছেন, যাঁরা দেখেছেন এই ফুল ফুটে ওঠা? কাদের চোখের
কাছে গাছ তার ফুলের ফুটে ওঠাকে সমর্পণ করেছে? প্রকৃতি সেই
নিবিড় লিখনমুহূর্তটি পাঠকের কাছে উন্মুক্ত করেছে। সেই পাঠক হতে চান রারাচৌ।
কেবলমাত্র দর্শন নেই এই রাণার কথায়। রয়েছে মাপসই মজাও, আনন্দ ও দুঃখভরা মেঘের পাশে চাঁদে পা ঝুলিয়ে এক মধ্যবয়স্ক বাঁকা হাসি হাসছে। যে হাসি নয়ের দশকের বাংলা
কবিতা বহু আগেই চিনে গিয়েছে। যাঁরা রাণা রায়চৌধুরীর মোটামুটি পাঠক, তাঁরা জেনে থাকবেন ওই পেয়ারাগাছের বেত দিয়ে সমাজকে সুড়সুড়ি দেওয়া।
অতলান্ত শোকের ভিতর তাঁর লেখায় স্বাভাবিকভাবেই চলে আসে ঠাট্টা। যে শোক ছিল
কবিতাবই ‘লাল পিঁপড়ের বাসা’য়–
হে মানুষ ভুল বুঝো না আমায়
আমি এখন রুটি বানাতে পারি
হে মানুষ ভুল বুঝো না আমায়
মা’র জন্য
শোক আমি আজও টিকিয়ে রেখেছি
সেই শোকের গায়েও হাসির ছ্যাঙড় জড়িয়ে জীবনগঙ্গায় ভেসে চলেছেন রারাচৌ।
হেঁটে চলেছেন পলতা স্টেশন ধরে, একা একা। লোকজন দেখতে দেখতে, মুদ্রাদোষ
ও মুদ্রাব্যবহার দেখতে দেখতে–
‘এক হাসপাতাল ফেরত বিকেলে একটা লাল রঙের স্টার আঁকা, ততোধিক লাল রঙের বিল্ডিঙের সামনে এসে প্রার্থনা করলাম– ‘আমার মাকে বাঁচাও ঠাকুর’– প্রণামের পর খেয়াল হল এটি
মন্দির নয়, সিপিএমের পার্টি অফিস।’
রারাচৌ আসলে রারাচৌ। কিংবা রারাচৌ রারাচৌ— এর মতো। প্রথম থেকেই দু’—চারখানা ছোটকাগজ বাদে ‘রাণার কথা’ না— বই হিসাবে বারেবারেই পড়ার সুযোগ, সৌভাগ্য হয়েছে আমার। রাণার কথা কি রারাচৌ— এর
আত্মজীবনী? আত্মপ্রলাপ? বিড়বিড় করা?
এই তত্ত্বজটিলতা ছেঁটে যদি দেওয়া হয় তাহলে রক্তমাংসের একজন সৎ মানুষকে
পাওয়া যায়। যে লিখব বলে ইতস্তত করেনি। মাত্র ৬০ পাতার এই বই, কিন্তু পড়া শুরু করলে কি কেবল রাণার কথাতেই টিকে থাকা যায়? পাঠকেরও স্মৃতিতেও কি ছোবল মারে না এই বই? কেবল
স্মৃতি নয়, বাস্তব নয়, স্বপ্নও এই
বইয়ের পাতার সঙ্গে জড়িয়ে। কুচুটে, আনন্দিত, দুঃখিত, কবি ও মানুষ রারাচৌ— এর
জীবনে ঢুকে পড়ার দু’মলাট এই বই। মিলবে বালকের মন নিয়ে পাখি
ওড়া রারাচৌ, পানু ছবি দেখার ইচ্ছে বয়ে বেড়ানো রারাচৌ,
কেবলমাত্র ছায়া দেখে আনন্দ পাওয়া রারাচৌ—কেও।
কয়েক বছর আগের একটি সাক্ষাৎকারে, মনে পড়ছে, রাণা
রায়চৌধুরীর বক্তব্য ছিল: বাংলা কবিতাকে আমি ডিস্টার্ব করতে এসেছি। ‘রাণার কথা’ পড়ার পর পুরনো সেই কথাসূত্র ধরেই বলতে
পারি: বাংলা আত্মজীবনীকে ডিস্টার্ব করতে এসেছে এই বই।
আঙ্গিক, বইমেলা সংখ্যা, ২০১৯





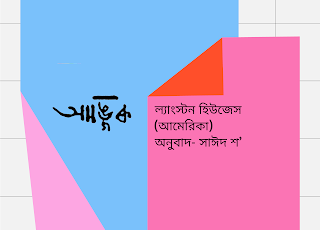
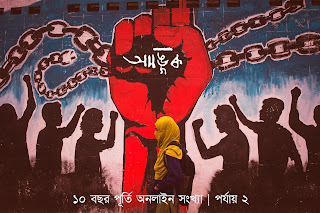
মন্তব্যসমূহ